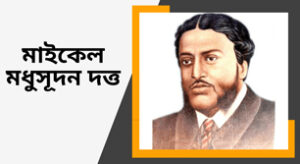র্যাগিং ও ছাত্রসমাজ:
র্যাগিং ও ছাত্রসমাজ
বাংলা প্রবাদে আছে ‘কাঙালী মেরে কাছারি গরম’–এই ঘটনায় লুকিয়ে আছে কৌতুকের নামে একধরনের অত্যাচার। জমিদার বাড়িতে রাজস্ব আদায়ের কারণে নানা লোকের সমাবেশ ঘটত। ফসল না হওয়ার কারণে খাজনা দিতে না পারলে কাঙালিদের ঠেঙিয়ে জমিদার মজা লুঠত। বেচারা যন্ত্রণায় যত ছটফট করবে, জমিদার ও মোসাহেবের দল ততই মজা পাবে। র্যাগিং-এর বাংলা অর্থ হল গোলমাল করা বা অত্যধিক হইহুল্লোড় করা বা কৌতুকের নামে অত্যাচার করা। বর্তমান ‘কাঙালী মেরে কাছারি গরম’-এর ব্যবস্থা না থাকলেও রয়ে গিয়েছে ‘ছাত্রছাত্রী মেরে ছাত্রাবাস গরম’ করার নানান ইতিহাস, যা কাম্য নয়। কারণ ছাত্রছাত্রীদের মূল কর্ম এবং ধর্মই সত্যিকার জ্ঞান অর্জন।
র্যাগিং হল একধরনের মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার। শিক্ষাবর্ষের সূচনায় কারিগরি ও মেডিকেল শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসগুলি র্যাগিং-কে কেন্দ্র করে অমানুষিক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। মজার ছলে পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা নবাগতদের জোর করে ধূমপান করতে বাধ্য করে, বিড়ি, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, মদ খাওয়ায় বাধ্য করে, শীতের দিনে পুকুরে বা নদীর জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে বলে। কখনও জামাকাপড় খুলে নেয়, অর্ধউলঙ্গ বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখে। অনেকসময় বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে গিয়ে এমন প্রশ্ন করা হয় যা মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যায়। মারধর, কিল-ঘুষি, গালাগালিতে ছাত্রছাত্রীরা অনেকসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফ্যালে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও র্যাগিং-এর প্রবণতা বাড়ছে। বন্ধু পরীক্ষার সময় উত্তর না দেখালে তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি বা মারধর চলে। দুর্বল ছাত্রের কাছ থেকে পয়সা বা টিফিন ছিনিয়ে নেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।
র্যাগিং-এর কারণ সম্পর্কে নানা জনের নানান অভিমত রয়েছে। কেউ বলেন, একদল মানুষের বিকৃত মানসিকতা এর কারণ। কেউ মনে করেন র্যাগিং স্বাস্থ্যকর, নবাগতদের পুরোনোদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কৌতুকের মাধ্যমে পারস্পরিক পরিচয়ের যোগসূত্র রচনা করা। একটু-আধটু ইয়ার্কি, ঠাট্টা-তামাশার মধ্য দিয়ে চিত্তবিনোদনের পথটা সহজেই খুলে যায়। এসব যুক্তি মেনে নেওয়া অসম্ভব। একে মানসিক বিকার বা পার্ভাসান বলা যেতেই পারে। সর্বোপরি র্যাগিং-এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, নীতি এবং আদর্শজনিত শিক্ষার অভাব। ধর্মের নামে র্যাগিং, রাজনীতির নামে র্যাগিং, আর্থিক কারণে র্যাগিং চলতে থাকে। কেউ বা স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছাত্রাবাসে দীর্ঘদিন পড়ে থেকে একাকিত্বের কারণে বিকৃতমনস্ক হয়ে পড়ে, অন্যকে র্যাগিং করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।
র্যাগিং এক সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির শিকার হয় গ্রাম কিংবা শহরের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। ভালো ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ বা নষ্ট করে দেওয়ার অন্যতম কৌশল এটি। এর ফলে কেউ সমাজ-শিক্ষা-আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া কাটিয়ে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়, কেউ বা সারাজীবন মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জীবন কাটায়, কেউ বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পরিবারের অযত্নে পড়ে থাকে। বর্তমানে বহু ছাত্রছাত্রী ছাত্রাবাসে থাকতে ভয় করে, তাই বাড়ির সামনে কোনো কলেজে পড়াশোনার ইচ্ছে প্রকাশ করে। র্যাগিং কৌতুকের নামে অত্যাচার, আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।
র্যাগিং নামক জঘন্য প্রথার অবসান হওয়া জরুরি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই শিক্ষার্থীদের নীতি-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠদানের সময় কমিয়ে বিকেলে খেলাধুলা, গানবাজনা, শিল্পকলার কাজ করার দিকে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তুলতে হবে। কলেজে ছাত্রাবাসে কড়া নজরদারির পাশাপাশি একই রুমে একই ক্লাসের বা বিষয়ের (subject) ছাত্রছাত্রী রাখা বন্ধ করতে হবে। র্যাগিং প্রতিরোধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এ ব্যাপারে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার। র্যাগিং বন্ধ করতে সত্যিকার শিক্ষা, মানবিকতার শিক্ষা, আর নিয়মশৃঙ্খলাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসন ও অনুশাসন প্রয়োজন।
র্যাগিং নির্মূলের প্রধান অন্তরায় ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব। এর পরিবর্তনে তিনটি জিনিসের অতি প্রয়োজন। আটিটিউড ছিল এবং নলেজ- এর উন্নতি। অ্যাটিটিউড-এর ‘এ’, স্কিল-এর ‘এস’ এবং নলেজ ইংরেজি শব্দের ‘কে’–একসঙ্গে যোগ করলে হবে ‘ASK’ অর্থাৎ জিজ্ঞাসা। এই আত্মজিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজন। অভিভাবক-অভিভাবিকা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আমজনতা সকলেরই আত্মজিজ্ঞাসার দরকার আছে। যদি আমরা আচরণ, দক্ষতা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারকে স্ফীত করতে পারি, তাহলেই র্যাগিং-এর অবসান সম্ভবপর হবে।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
উনিশ শতকের একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পাণ্ডিত্য, দয়াপরায়ণতা এবং তেজস্বিতায় তিনি সমকালীন যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাংলার সমাজসংস্কার ও সাহিত্যসংস্কারে তাঁর অবদান অপরিসীম।
‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। অন্য অনেকের মতো গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যারম্ভ। একটু বড়ো হলে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় আসার সময়ই তাঁর পিতা বিদ্যাসাগরের অসাধারণ মেধার পরিচয় পান রাস্তায় মাইলস্টোন গণনার ঘটনায়। কলকাতায় এসে পিতা তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভরতি করে দেন। সংস্কৃত কলেজে প্রায় বারো বছর পড়াশোনা করে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি-সহ বহু ভাষা শেখেন ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরই পাশাপাশি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পরিসীমাহীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষর পদ অলংকৃত করেন। অধ্যক্ষ থাকাকালীন সংস্কৃত কলেজে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকারকে স্বীকৃতি দেন।
বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম মাইলস্টোন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন। ‘বাসুদেব চরিত’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘শকুন্তলা, ‘সীতার বনবাস’, ভ্রান্তিবিলাস’ ইত্যাদি তাঁর অনুবাদমূলক রচনা। এগুলি অনুবাদ গ্রন্থ হলেও এতে অনুকরণ নয়, লেখকের মৌলিক প্রতিভারই পরিচয় পরিস্ফুট। ছোটোদের জন্য তিনি ‘বোধোদয়’, ‘কথামালা’, ‘আখ্যানমঞ্জুরী’ ইত্যাদি রচনা করেন। তিনি ছদ্মনামে ‘অতি অল্প হইল’, ‘আবার অতি অল্প হইল’-সহ বহু ব্যঙ্গমূলক রচনা লেখেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষাকে সহজসরল, সাবলীল, সকলের পাঠ-উপযোগী করে তোলেন। বাংলা গদ্যে প্রথম দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহারে বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলার কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য।
পণ্ডিত বিদ্যাসাগর ছিলেন দৃঢ়চেতা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। তিনি নিজে যেটি ঠিক বলে মনে করতেন সেই সংকল্প থেকে তাঁকে নড়ানোর কোনো ক্ষমতা কারোর ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাঁর পিতা তাকে যেদিন স্নান করতে বলতেন সেদিন তিনি কিছুতেই স্নান করতেন না, পরিষ্কার বস্ত্র পরে তাঁকে স্কুলে যেতে বলা হলে তিনি অপরিষ্কার কাপড় পরতেন। এই জেদ পরবর্তীকালে তাঁর সমাজসংস্কারমূলক কাজে লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে মাতা ভগবতী দেবীর কাছ থেকে তিনি অপরিসীম দয়া ও নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করার মহৎ গুণ পেয়েছিলেন। তিনি নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও করুণাতেই শাস্ত্র থেকে প্রমাণাদি গ্রহণ করে কৌলীন্য প্রথার বিরোধিতা করেন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ করেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন করেন। নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (বেথুন স্কুল) স্থাপন করেন। এই সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক কাজে তিনি যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করেন সেগুলি ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতবিষয়ক প্রস্তাব’, ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ ইত্যাদি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন।
উনিশ শতকে বাংলার সমাজসংস্কার, সাহিত্য সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবশ্যস্বীকার্য। কালের যাত্রাপথে এই মহান ব্যক্তি দ্বিশতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। সমগ্র দেশ সেই উদ্যাপনে উন্মুখ। যদিও প্রশ্ন জাগে বর্তমান সমাজ তাঁকে কতটা জানল, কতটা বুঝল। বাংলার ‘দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই পরলোকগমন করেন।
চন্দ্রযান 3:
চন্দ্রযান 3
ভূমিকা : চন্দ্রযান ৩ হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) -এর দ্বারা পরিচালিত অন্যতম বিখ্যাত একটি চন্দ্র অভিযান। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এর বিজ্ঞানীগণ চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণস্থল হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে বেছে নিয়েছে। এর অত্যাধুনিক যন্ত্রগুলি চন্দ্রের মাটি তদন্ত করার জন্য এবং মূল তথ্য চাঁদ থেকে প্রথিবীতে পাঠানোর জন্য সেট করা হয়েছে। এই চন্দ্র অভিযান মিশনের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে। যথা – একটি অরবিটার, বিক্রম নামক একটি ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা দ্বারা চন্দ্র অভিযান এর তৃতীয় মিশন করার পিছনে মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, চাঁদের মাটিতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবতরণ, রোভারের নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সক্ষমতা যাচাই এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
পটভূমি : ভারতের প্রথম চন্দ্র অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল চন্দ্রযান ১ মহাকাশযান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। যেটি 2008 সালে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছিল এবং ভারতকে চাঁদের আশেপাশে প্রদক্ষিণ করার জন্য চতুর্থ দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। এরপর চন্দ্রযান ২ মহাকাশযান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, এর সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জের পর, 14 জুলাই, 2023-এ চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানকে চন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করার উদ্যেশ্যে ভারতের একটি বিশিষ্ট মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র সতীশ ধবন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।
চন্দ্র অভিযানের লক্ষ্য : এই মিশনের উদ্দেশ্য হল চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল এবং নিরাপদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
চন্দ্রযানের উপাদান : চন্দ্রযান মিশনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, ল্যান্ডারে বেশ কিছু উন্নত প্রযুক্তি বা উপাদান রয়েছে যেমন লেজার এবং আরএফ-লিডি অল্টিমিটার, ভেলোসিমিটার, প্রপালশন সিস্টেম ইত্যাদি।
চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ : 2023 সালের 14 জুলাই ভারতের সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সময় ২ টো ৩৫ মিনিটে চন্দ্রযান-৩ সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এই মহাকাশযানকে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা জন্য L.V.M 3 রকেটের ব্যবহার করা হয়েছিল।
চন্দ্রযানের অবতরণ : মহাকাশের মধ্য দিয়ে এক মাসব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পর, মহাকাশযানটি 2023 সালের 23ই আগস্ট তার গতিপথ অতিক্রম করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড বা অবতরণ করেছিল। এই সময় মহাকাশযানটি চাঁদের 164 কিমি X 18074 কিমি কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল। সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে ল্যান্ডার বিক্রম অবতরণ করে। এই অবতরণ প্রায় 19 মিনিট ধরে চলেছিল।
অভিযানের আর্থিক ব্যয় : এই চন্দ্র অভিযানটি প্রায় 615 কোটি টাকা খরচে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আর অভিযানের এই আর্থিক ব্যয় অন্যান্য দেশের থেকে অনেক কম।
ল্যান্ডিং পয়েন্টের নামকরণ : চন্দ্রযানটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুর যে জায়গায় অবতরণ করেছে সেই জায়গাটির নামকরণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘শিব শক্তি’।
ভারতের স্থান : এই মিশনটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, ভারতবর্ষ একমাত্র প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে, সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার দেশ হিসাবে এবং চাঁদে অবতরণ করা চতুর্থ তম দেশ হিসাবে ভারত বর্তমানে স্থান পেয়েছে।
চন্দ্রযান-3 বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ : চন্দ্রযান ৩-এর ধারণাটি বাস্তবায়নে বেশ কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন – এস সোমনাথ (ইসরো চেয়ারম্যান), পি ভিরামুথুভেল (চন্দ্রযান-৩ এর প্রকল্প পরিচালক), এস উন্নিকৃষ্ণান নায়ার (বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের পরিচালক), এ রাজারাজন (লঞ্চ অথরাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান), এম শঙ্করণ (ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টারের পরিচালক)প্রভৃতি।
উপসংহার : 2023 সালের 23 শে আগস্ট দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ চন্দ্রযান মিশনটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ এবং চন্দ্র অবতরণ অর্জনের জন্য চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারতকে মুকুট দিয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে খুব কম বাজেট 615 কোটি টাকার মধ্যে সফল ভাবে এই চন্দ্র অভিযানটি সম্পন্ন হয়েছে।
গঙ্গা দূষণ: সমস্যা ও প্রতিকার
গঙ্গা দূষণ: সমস্যা ও প্রতিকার
ভূমিকা: গঙ্গা নদী শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, এবং জীবনধারার প্রতীক। গঙ্গার তীরেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের মহান সভ্যতাগুলি। তবে আজকের দিনে এই পবিত্র নদী, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রার অংশ ছিল, দূষণের কারণে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। একসময়ের প্রাণদায়িনী গঙ্গা আজ মানুষের অসচেতনতা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্যকলাপের কারণে নিজেই দূষণের শিকার হয়েছে।
গঙ্গার উৎপত্তি ও পৌরাণিক গুরুত্ব
গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে, যেখানে এটি ভাগীরথী নামে পরিচিত। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, রাজা ভগীরথের তপস্যার ফলে গঙ্গা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এই কাহিনী গঙ্গার পবিত্রতা এবং তার আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। ভৌগোলিক দিক থেকে গঙ্গা ভারতবর্ষের দীর্ঘতম নদী, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫২৫ কিমি এবং এটি হিমালয়ের কোলে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।
গঙ্গার গতিপথ ও তার গুরুত্ব
গঙ্গার তিনটি প্রধান গতিপথ রয়েছে: উচ্চগতি, মধ্যগতি, এবং নিম্নগতি। উচ্চগতি হল গঙ্গোত্রী থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত, মধ্যগতি হল উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্যে, এবং নিম্নগতি হল পশ্চিমবঙ্গের সীমানা দিয়ে যেখানে এটি ভাগীরথী এবং পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা নদী শুধুমাত্র ভারতের কৃষি, শিল্প, এবং পানীয় জল সরবরাহের প্রধান উৎস নয়, এটি দেশের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনধারারও প্রতীক।
গঙ্গা দূষণের কারণ
গঙ্গা নদীর দূষণের প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ:
- শহরের বর্জ্য: নগরগুলির অপরিশোধিত বর্জ্যপদার্থ এবং গৃহস্থালি মলমূত্র সরাসরি গঙ্গায় ফেলার ফলে নদীর জল ভয়ানকভাবে দূষিত হচ্ছে।
- শিল্প দূষণ: কল-কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক এবং বর্জ্য পদার্থ গঙ্গার জলে মিশে নদীর জৈবিক ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করছে।
- কৃষি দূষণ: কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের অবশিষ্টাংশ এবং কীটনাশক বৃষ্টির জল দিয়ে গঙ্গায় এসে মিশে দূষণকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।
- নির্মাণ ও পলি জমা: নদীর তীরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কাজ এবং নদী বাহিত পলিমাটি গঙ্গার নাব্যতা কমিয়ে দিচ্ছে।
- মানবিক কার্যকলাপ: গঙ্গার তীরে কাপড় কাচা, পশু স্নান, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ফলে গঙ্গার জলে জীবাণু এবং অন্যান্য দূষণ পদার্থের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।
- উৎসব ও পবিত্র স্নান: হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, গঙ্গায় স্নান করা পাপ মুক্তির উপায়। কিন্তু গণস্নানের সময় প্রচুর পরিমাণে দূষণ পদার্থ নদীতে মিশে দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।
- পর্যটন ও পর্যটকদের কার্যকলাপ: গঙ্গার তীরে পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং মানুষের অসচেতনতা গঙ্গা নদীর দূষণকে আরও জটিল করে তুলছে।
গঙ্গা দূষণের প্রভাব
গঙ্গা দূষণের পরিণাম অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং বহুমুখী:
- জলমানের অবনতি: গঙ্গার জলমানের ক্রমাগত অবনতি ঘটছে, যা পানীয়, কৃষি, এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে।
- জলজ জীববৈচিত্র্যের হ্রাস: গঙ্গার দূষণ জৈবিক বৈচিত্র্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বহু প্রজাতির মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী প্রায় লুপ্তির পথে।
- স্বাস্থ্যগত প্রভাব: দূষিত গঙ্গার জল পান করার ফলে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগব্যাধি যেমন ডাইরিয়া, টাইফয়েড, এবং হেপাটাইটিসের প্রকোপ বাড়ছে।
- পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা: গঙ্গার দূষণ মাটির উর্বরতা এবং ভূগর্ভস্থ জলের মানকেও প্রভাবিত করছে, যা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: গঙ্গা নদীর দূষণ সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্যচাষ, এবং পর্যটন শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা এলাকার অর্থনীতির ক্ষতি করছে।
গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ
গঙ্গার দূষণ প্রতিরোধে ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৮৬ সালে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল গঙ্গার জলের গুণমান উন্নত করা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কিছু প্রধান কার্যক্রম ছিল:
- অপরিশোধিত বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ: শহর এবং শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য গঙ্গায় ফেলার আগে তা পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শ্মশান এবং ঘাটের উন্নয়ন: শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা এবং স্নানের ঘাটগুলি সংস্কার করা হয়েছে।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি: গঙ্গা দূষণ রোধে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে।
- নমামি গঙ্গে প্রকল্প: ২০১৪ সালে গঙ্গা নদী পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নমামি গঙ্গে প্রোগ্রাম চালু করা হয়, যা এখনো কার্যকর রয়েছে।
উপসংহার: গঙ্গা নদী শুধুমাত্র একটি জলাধার নয়, এটি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশ। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত এবং তার আধ্যাত্মিক মহিমাকে পুনরুদ্ধার করা শুধুমাত্র আমাদের পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় গর্বের বিষয়। আমাদের সকলের দায়িত্ব হলো গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। গঙ্গার সংরক্ষণ একটি জাতীয় কর্তব্য, যা শুধু পরিবেশের সুরক্ষার নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণও নিশ্চিত করবে।
যুবসমাজ ও অপরাধপ্রবণতা:
যুবসমাজ ও অপরাধপ্রবণতা
যুবসমাজ একটি দেশের সম্পদ, ভবিষ্যতের নেতৃত্ব। কিন্তু আজকের দিনে, যুবসমাজের এক অংশ অপরাধপ্রবণতার দিকে ঝুঁকছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে। অপরাধপ্রবণতা যুবসমাজের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা শুধু যুবসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে পড়ছে। তাই যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতা একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
অপরাধপ্রবণতার কারণ:
যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতার পিছনে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। এগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং মনস্তাত্ত্বিক হতে পারে।
- বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাব: অনেক যুবক-যুবতী অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। চাকরির অভাব এবং অর্থনৈতিক সংকট তাদেরকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। সহজ আয়ে জীবনযাপনের লোভে তারা চুরি, ডাকাতি, মাদক পাচার, এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।
- পারিবারিক সমস্যা ও বিচ্ছিন্নতা: পারিবারিক অস্থিরতা, বিচ্ছেদ, এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ যুবসমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। অনেক সময় পারিবারিক সহিংসতা, অবহেলা, এবং দারিদ্র্য যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা তাদেরকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত করে।
- অশিক্ষা ও সামাজিক অবক্ষয়: শিক্ষার অভাব এবং নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে যুবসমাজ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, অনৈতিকতা, এবং সাংস্কৃতিক চর্চার অভাবও যুবকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে।
- মাদকের প্রভাব: মাদকাসক্তি অপরাধপ্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ। মাদক গ্রহণের ফলে যুবসমাজ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। মাদকের লোভে তারা চুরি, ডাকাতি, এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- প্রযুক্তির অপব্যবহার: বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অপব্যবহার যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, সাইবার অপরাধ, এবং অনলাইন প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যুবসমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অপরাধপ্রবণতার ফলাফল:
যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতার ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- সামাজিক অস্থিরতা: অপরাধপ্রবণতার কারণে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ বাড়ছে এবং সমাজে অবিশ্বাস ও হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে।
- শিক্ষা ও কর্মজীবনে ব্যাঘাত: অপরাধে জড়িয়ে পড়া যুবকদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে ব্যাঘাত ঘটে। তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মজীবন গড়ে তোলার সুযোগ হারায়।
- আইনি প্রক্রিয়া ও শাস্তি: অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে যুবকদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয় এবং তারা পুনর্বাসনের সুযোগও হারায়।
- পরিবারের ওপর প্রভাব: যুবকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে তাদের পরিবারের ওপরও মানসিক, আর্থিক এবং সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়। পরিবারের সম্মানহানি ঘটে এবং সমাজে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়।
প্রতিরোধ ও সমাধান:
যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতা রোধে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: শিক্ষার মাধ্যমে যুবসমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখা সম্ভব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।
- পরিবারের সমর্থন: পরিবারকে যুবকদের মনোভাব ও কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং তাদের মানসিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করতে হবে।
- মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন: মাদকের প্রভাব থেকে যুবসমাজকে বাঁচাতে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। মাদক বিরোধী প্রচারাভিযান এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।
- চাকরির সুযোগ সৃষ্টি: সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পেলে যুবকরা অপরাধের দিকে ধাবিত হবে না।
- সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা: বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন যুবসমাজকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে সচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ড চালাতে পারে। এই ধরনের সংগঠনগুলি যুবকদের পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।
উপসংহার: যুবসমাজের অপরাধপ্রবণতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যা, যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা, সচেতনতা, এবং সামাজিক সমর্থনের প্রয়োজন। যুবসমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে হলে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে এবং তাদের সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যুবসমাজকে অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করা শুধুমাত্র তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য নয়, সমাজের শান্তি, স্থিতি, এবং উন্নতির জন্যও অত্যন্ত জরুরি। যুবকদের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে, তারা দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, এবং সমাজে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
বাংলার উৎসব:
বাংলার উৎসব
ভূমিকা: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই বাঙালির উৎসবের শেষ নেই। আসলে বাঙালির মানসিকতা হল দূরকে নিকট করা। এই আস্তরিকতার গুণেই সবাইকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠতে চায় বাঙালি। শত দুর্যোগ-দুর্বিপাকে, শোষণে অত্যাচারেও বাঙালির উৎসবপ্রিয় মানসিকতার ভাটা পড়েনি। সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই বলেছিলেন — “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।” শুধু তাই নয়, বাঙালির উৎসবের বৈচিত্র্যও যথেষ্ট।
উৎসব কী: রবীন্দ্রনাথ ‘উৎসব কি’–এ প্রসঙ্গে বলেছেন—“মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, … উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করে মহৎ।”
উদ্দেশ্য: মানুষ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে ক্ষুদ্র কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহৎ। মানুষ তার সংসার চক্রের নিরানন্দময় জীবন থেকে বাঁচবার জন্য, নিজেকে অপরের কাছে প্রকাশ করবার জন্য, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসে উৎসবের আয়োজন করেছে। উৎসবের দিনে মানুষ যেহেতু সমস্ত ক্ষুদ্রতা, হীনতা, ক্লীবতার গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারে, তাই সেদিন মানুষ নিজেকে অপরের মধ্যে খুঁজে পায় বলে সেদিন আনন্দের দিন। বাঙালির উৎসব তাই আনন্দ সংগীতেরই সমারোহ।
উৎসবের বিবর্তন: বৈদিক ঋষিদের সোমরস নিষ্কাশনের এক আনন্দ-উদ্বেল লোকাচার ছিল উৎসব। অন্য দিকে আদিম মানুষও শিকারের শেষে নির্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরে এসে দলবদ্ধ হয়ে আগুন জ্বালিয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতো। তারপর সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ উৎসবের ক্ষেত্রে আরো বেশি আন্তরিক হয়ে উঠছে। মানুষ উৎসবকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। তবে আগে উৎসবের মধ্যে একটা আলাদা মাহাত্ম্য ছিল। কারণ আগে উৎসবের সঙ্গে কল্যাণবোধ ও মঙ্গলবোধ জড়িত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ বড্ড বেশি যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। সমাজে মানুষের প্রাচুর্যতার মধ্যেকার সত্তাকে করেছে বিনষ্ট। দুর্নীতি, অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা মানুষের সম্পর্কের মধ্যে দেওয়াল তৈরি করেছে। আড়ম্বর ও অহংকারের মধ্যে বিলুপ্ত হতে বসেছে উৎসবের গুরুত্ব। এখন যেটুকু আছে, তা লোক দেখানো। উৎসব এখন বিপণনে পরিণত হয়েছে।
বাঙালির উৎসবপ্রিয়তা: বাঙালির উৎসবের প্রেরণা মজ্জাগত। অবশ্য সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসবের মৌল প্রেরণা সম্বন্ধে কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি : (১) ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তির পথ খোঁজা। (২) পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষা। (৩) ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা। (৪) প্রাণের আনন্দ আস্বাদনের ইচ্ছা। (৫) কর্মময় জীবনের সাফল্যের স্বীকৃতি। যেমন, আদিম মানুষ শিকার সেরে এসে উৎসবে নিজেদের মুখরিত করতো। এখনো কোনো কোনো। উপজাতির মধ্যে দেখা যায় উৎসবের সময় তারা পশুবলি দিয়ে উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। কৃষিজীবনেও ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ‘নবান্ন’, ‘পৌষ পার্বণে’র উৎসব। সুতরাং ‘সর্বজনীন কল্যাণময় ইচ্ছা-ই’ উৎসবের মূল প্রেরণা।
উৎসবের বৈচিত্র্য: বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই তাদের উৎসবের বৈচিত্র্যকে সূচিত করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধর্মাচরণ, জীবনধারার বৈচিত্রানুযায়ী উৎসবের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন:- জাতীয় উৎসবগুলিতে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে নানান স্মরণ অনুষ্ঠান। সেগুলি হল—স্বাধীনতা উৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব, গান্ধীজির জন্ম দিবস উদ্যাপন, নেতাজির জন্ম দিবস উদযাপন ইত্যাদি।
সামাজিক উৎসব: বাঙালির উৎসবের মধ্যে সামাজিক উৎসব-ই সব থেকে বেশি। এই শ্রেণির উৎসবে সমাজের মানুষ বেশি করে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এইসব উৎসব হল বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, জন্মদিন পালন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা ইত্যাদি।
ধর্মীয় উৎসব: বাঙালির ধর্মীয় চেতনা মজ্জাগত। যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাদের মধ্যে থাকে উৎসবের মেজাজ। যে কোন ধর্মের লোকেরাই যে কোন ধর্মের অনুষ্ঠানে নিজেদেরকে আনন্দে মাতিয়ে রাখে। বিশেষ করে বাঙালির দেবদেবীর অস্ত্র নেই। বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গোৎসব। সমগ্র বাংলায় এই উৎসব আলাদা আমেজ নিয়ে আসে। দুর্গাপূজায় বাঙালি শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসঙ্গে মিশে আনন্দ করে। তাছাড়া রয়েছে বাসন্তী পূজা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উৎসব জন্মাষ্টমী, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব, ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা এবং নানা সময়ে হরিনাম সংকীর্তন, দোল উৎসব, রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, শিব চতুদশী ও শিবের গাজন উৎসব এবং আরো কত কী। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানদের সেরা উৎসব ঈদ। ঈদ মিলনের উৎসব। সেই সঙ্গে মহরম ও অন্যান্য উৎসব। খ্রীস্টানদের বড়দিন ও গুডফ্রাইডে বড় উৎসব। বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা, শিখদের গুরু নানকের জন্মদিনও ধর্মীয় উৎসব। বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে সব ঋতুতে বাঙালি বিভিন্ন ঋতু উৎসব পালন করে।
লোক উৎসব: বাংলায় নানান ধরনের লোক উৎসব প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ করে বাংলার আদিবাসী জনজীবনে এইসব লোক উৎসব আজও আদিম সংস্কৃতির স্বরূপকে টিকিয়ে রেখেছে। অঘ্রাণে ধান ওঠার উৎসব নবান্ন উৎসব, পৌষে শস্যসম্ভারে ঘর ভরে ওঠার পর পিঠে পার্বণ ও তুষ তুষালি উৎসব। এছাড়া বর্ধমান,বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে পালিত হয় শস্যের লোক উৎসব। যেমন—’ভাদু’, ‘টুসু, ইতু’ ইত্যাদি।
উৎসবের মূল্যায়ন: বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি যেখানে পাল্টে যাচ্ছে সেখানে উৎসবের যে পরিবর্তন হবে—তা বলাবাহুল্য। এখন উৎসবও মার্কেট বা বিপণনকেন্দ্রিক। একথা ঠিক, উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু বৃত্তিজীবী মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়। এদিক থেকে উৎসবের একটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু পূর্বে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ একত্র মিলিত হত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, বাংলার উৎসবের
মধ্যে এখন আর সেই একাত্মতা, সেই আন্তরিকতা নেই। তার পরিবর্তে আছে আড়ম্বর, জৌলুস ও কৃত্রিমতা। ফলে বর্তমানে উৎসবের মধ্যে সেই পূর্ণতাবোধ নেই।
উপসংহার: বাঙালির উৎসবের মূল চেতনা ছিল— দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।’ কিন্তু তা আর এখন নেই, নেই পারস্পরিক কল্যাণ কামনা। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা দর্শনের থেকে বড় হয়ে ওঠে কে কোন্ পোশাক বা অলংকার পরেছে তা দেখা, কিম্বা নিজেকে কে কতটা জাহির করতে পারে তার অবৈধ প্রতিযোগিতা। তাই উৎসবের গুরুত্ব স্নান হয়ে গিয়ে আনন্দকে করছে খণ্ডিত এবং মানুষের আত্মার শান্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। তাই বাংলার উৎসব আবার সেই মিলন, মৈত্রী ও শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে আসুক—উৎসব- পাগল বাঙালির এই হোক অন্তরের কামনা।
রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ
রাজা রামমোহন রায়
ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত তথা বঙ্গদেশ যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ও সামাজিক কুপ্রথার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে বাংলার আকাশে এক আলোকিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যিনি শুধু সমাজসংস্কারক হিসেবেই নয়, বরং জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়। তাঁর অসামান্য শৌর্যবীর্য, দৃঢ় প্রত্যয় ও অগাধ পাণ্ডিত্য বাংলার সমাজকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।
জন্ম ও শিক্ষাজীবন
রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২ সালের ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ এবং মা তারিণী দেবী ছিলেন গৃহলক্ষ্মী। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। পরে পাটনায় আরবি ও ফারসি ভাষা শিখে তিনি ইসলামি সংস্কৃতি ও দর্শনের ওপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া, ইংরেজি, গ্রিক, ও হিব্রু ভাষার প্রতি তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল, যা তাঁকে বিশ্বজনীন মানসিকতা গঠনে সহায়ক হয়েছিল।
কর্মজীবনের শুরু
রামমোহন রায় ১৭৯৬ সালে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং মহাজনের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। পরে, ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি রংপুরে একজন দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হন। যদিও, এই চাকরি তাঁকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করেছিল, তবু তাঁর মন সদা সমাজসংস্কারের দিকে আকৃষ্ট ছিল। ফলে তিনি পরবর্তীকালে সমাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন।
সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজ
রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের কাজের মূলে ছিল মানবতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান। ১৮১৫ সালে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নিজস্ব গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম চালিয়ে যান। এই সময়ে তিনি ফারসি ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গ্রন্থ “তুহফাতুল মুহাহাহিদিন” প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি একেশ্বরবাদ দর্শনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। এরপর তিনি আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে ব্রাহ্মসমাজ হিসেবে বিকশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রচার করেন এবং সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেন।
সতীদাহ প্রথা বিলোপ
রামমোহন রায়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। এই বর্বর প্রথা অনুযায়ী, হিন্দু বিধবা নারীদের তাঁদের মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় পুড়ে মরতে হত। রামমোহন যুক্তিনির্ভরভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, এই প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার ফল। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও জনসভার মাধ্যমে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথাকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই আইনের প্রবর্তন ভারতীয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে দেয়, যা নারীর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।
শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান
রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ১৮১৭ সালে তিনি ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজকের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসূরি। এছাড়া, ১৮২২ সালে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং ১৮২৬ সালে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর শিক্ষানুরাগী মানসিকতার প্রতিফলন। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব এবং তাঁর এই ধারণা পরবর্তীকালে অনেক শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকের প্রেরণা হয়ে ওঠে।
রাজনৈতিক সচেতনতা ও ব্রিটেনে সফর
রাজা রামমোহন রায় শুধু সমাজসংস্কারক হিসেবেই নয়, একজন দক্ষ কূটনীতিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩০ সালে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবরের দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। তাঁর এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত আইনটিকে বহাল রাখা। ইংল্যান্ডে তিনি উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর সম্মানে মোগল বাদশা তাঁকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত করেন।
মৃত্যু ও উত্তরাধিকার
১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় ব্রিস্টলের কাছে স্ট্যাপল্টন অঞ্চলে ম্যানিনজাইটিসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তিনি সমাজে এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকেন। ব্রিস্টলে তাঁর সমাধি আজও রয়েছে, যা তাঁর স্মৃতিকে জীবিত রাখে। ব্রিটিশ সরকার তাঁর সম্মানে ব্রিস্টলের একটি রাস্তার নামকরণ করেছে “রাজা রামমোহন ওয়ে।”
উপসংহার
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ ও আধুনিক ভারতের জনক। তিনি যে গদ্যের রূপ দিয়েছিলেন, তা আজকের বাংলা ভাষার ভিত্তি। একই সঙ্গে, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা, সাহসী অবস্থান ও নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের জাতির মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তাঁর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আজও অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে যথার্থভাবেই অভিহিত করেছিলেন “ভারতপথিক” নামে, যা তাঁর জীবনের মূল ভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে সংক্ষেপে তুলে ধরে।
সমাজ জীবনে মেলার প্রয়োজনীয়তা:
সমাজ জীবনে মেলার প্রয়োজনীয়তা
“মেলা” শব্দটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ অর্থবহন করে। এটি কেবল একটি জমায়েত নয়; বরং এটি হলো সংস্কৃতি, ইতিহাস, এবং মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্যের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। মেলা হচ্ছে সেই মিলনক্ষেত্র যেখানে মানুষের আবেগ, অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনার অর্গল ভেঙে যায় এবং এক নতুন সমাজচেতনা জন্ম নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে যেমনটি উল্লেখ করেছেন, “মেলা আমাদের সমাজের জন্য একটি অমূল্য উপহার, যা মানুষকে মানুষের কাছাকাছি আনার জন্য এবং সংকীর্ণতাকে দূর করার জন্য অপরিহার্য।”
উৎস ও ঐতিহ্য: ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে মেলার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। মানুষ যখন একান্তভাবে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন থেকেই মেলা তাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল। একত্রিত হওয়ার, ভাব বিনিময়ের, এবং আনন্দের এক সহজ উপায় হিসেবে মেলা গড়ে উঠেছিল। এই মেলাগুলি শুধুমাত্র বিনোদন বা বাণিজ্যিক লেনদেনের জায়গা ছিল না; বরং এটি ছিল কুসংস্কার, সংকীর্ণতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তির একটি পথ। মেলার মাধ্যমে মানুষ প্রথমে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে শিখেছে, যা তাদের মনকে প্রসারিত করেছে এবং নতুন ধারণার জন্য উন্মুক্ত করেছে।
সামাজিক গুরুত্ব: মেলার সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মেলার মধ্য দিয়ে মানুষ একত্রিত হয় এবং সংস্কার, ধর্ম, জাতিভেদ, এবং শ্রেণিভেদ ভুলে একসঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলনের মধ্য দিয়ে সমাজে একধরনের নতুন চেতনা জন্ম নেয়, যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও গভীর করে তোলে। মেলা আমাদের সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঐতিহ্য এবং সংস্কারকে বহন করে।
অর্থনৈতিক গুরুত্ব: মেলা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মেলার মাধ্যমে তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন এবং বিক্রি করতে পারেন। এটি তাদের জন্য একটি বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, যেখানে তারা তাদের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে মেলার গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এখানে কৃষিপণ্য, হস্তশিল্প, এবং স্থানীয় সামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা যায়।
সাংস্কৃতিক প্রভাব: মেলা একটি সংস্কৃতির মহোৎসব, যেখানে লোকনৃত্য, গীত, নাটক, এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। এটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা সমাজের মধ্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করে। মেলার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একত্রিত হয় এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, যা সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে।
আধুনিক প্রেক্ষাপটে মেলা: বিশ্বায়নের যুগে মেলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। মেলা এখন শুধু স্থানীয় সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বৈশ্বিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মেলা আজকের দিনে বিনোদন এবং সামাজিক মিলনের পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ তাদের পণ্য এবং সংস্কৃতি প্রদর্শন করে। তবে, এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে মেলার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না যায়, সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
উপসংহার: মেলার প্রয়োজনীয়তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপরিসীম। একদিকে, এটি মানুষের মনকে প্রসারিত করে এবং নতুন চিন্তা-ভাবনার জন্য উন্মুক্ত করে; অন্যদিকে, এটি সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং সমাজের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতাকে দূর করে। তবে বর্তমানের বাণিজ্যিকীকরণের যুগে মেলার প্রকৃত গুরুত্ব এবং তার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না যায়, সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, মেলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আমাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়।
একটি গ্রাম্য মেলা:
একটি গ্রাম্য মেলা
ভুমিকা: “কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি বুলি /মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি ” বাস্তবিক বাঙালির নান্দনিক দিকের পরিচয় কীর্তন ও বাউলগানে। বাউলরা উদাসী, সংসারত্যাগী ও মানবতাবাদী, তারা মানুষের কথা বলেন। এই বাউলদের সমাবেশ ঘটে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে বীরভূম জেলার কেন্দুবিশ্ব গ্রামে অজয় নদীর তীরে। সেই উপলক্ষে শুধু বাউল নয়, বহু মানুষের জনসমাগম ঘটে ঐ প্রসিদ্ধ জায়গায়।
বাউল মেলা: অজয়ের তীরে এই বাউল মেলাকে জয়দেব স্মরণোৎসবও বলা হয়। প্রসিদ্ধ কবি ও ‘গীতগোবিন্দ’ রচয়িতা কবি জয়দেব কোনো কোনো গানের ভণিতায় নিজেকে ‘কেন্দুবিশ্বসম্ভব রোহিণীরমণ’ বলে উল্লেখ করেছেন, এই উল্লেখ এবং আনুষঙ্গিক জনশ্রুতির মাধ্যমে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত ইলামবাজারের অন্তর্গত কেন্দুলি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কিম্বদন্তী আছে, পৌষ সংক্রান্তির দিনে ভক্ত জয়দেব সুদূর কাটোয়ায় হেঁটে যেতেন, গঙ্গায় পুণ্যস্নানের জন্য। তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তি গঙ্গাকে বিচলিত করে। গঙ্গা জয়দেবকে জানান, বছরে একটি দিন পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি অজয়ের সঙ্গে যুক্ত হবেন। জয়দেব সেদিন ঐখানেই স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জিত হবে। গঙ্গার আগমনের নিদর্শন চিহ্নিত করা যাবে ঐদিন অজয়ের স্রোতকে উজানে যেতে দেখে। এই জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করে পৌষ সংক্রান্তিতে বাউল মেলা অনুষ্ঠিত হয়—অজয়ের তীরে।
উৎসবের দিনের বর্ণনা: উৎসবের দিনে সকাল থেকে বহু পুণ্যার্থী মানুষ এখানে সমবেত হয়। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ বাউল গানের মধ্যে। বহু জায়গা থেকে বাউলরা এসে মিলিত হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মিলনের মন্ত্রে সবাই সেখানে ঐ দিন একত্রিত হয়। বাউলরা গুণিযন্ত্র সহকারে গান গাইতে থাকেন। বিদেশ থেকেও বহু মানুষ এই বাউলদের সমাবেশ দেখার জন্য উপস্থিত হয়। এবং তারা টেপে তাদের গান রেকর্ড করে নিয়ে যায়। ছোট ছোট জটলায় বিভক্ত হয়ে বাউলরা আখড়ায় সমবেত হয়। সারাদিন অবিশ্রাম চলে বাউলের নাচ ও গান। রঙ-বেরঙের জোড়াতালি দেওয়া আল খাল্লা, ঘুঙুর আর গুপিযন্ত্রের তালে তালে ভেসে আসে – ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়।’
অভিজ্ঞতা: সারা দিনরাত ধরে উৎসব চলার পর তা শেষ হয়। জেগে থাকে বুক ভরা স্মৃতি। শীতের দুঃসহ প্রবাহের মধ্যে বহু মানুষের কলকল্লোল, বাউলের নাচের ভঙ্গি আর কণ্ঠ-নিঃসৃত উদাসী গান— মানুষের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়। বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক অপরূপ আলেখ্য রচিত হয় প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন। অজয়ের তীরে এই বাউল মেলায়।
স্মরণীয় হওয়ার কারণ: আমরা জানি, মেলা হল মিলন–এই মিলন মানুষে-মানুষে। জাতপাত, শ্রেণি, ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হওয়া ও পরস্পর আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে উদ্দীপিত করা হল যে কোন মেলার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন-“আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে করে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।” সুতরাং মেলা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে একটি অপরিহার্য। উপাদান। যেখানে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার একটি সুযোগ উপস্থাপিত হয়। সেদিক থেকে। এই বাউল মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে সমাজে ও সংস্কৃতিতে যখন প্রথাবদ্ধতা বা কূপমণ্ডুকতা এসেছে তখন সূফী সাধক, বাউল ফকিররা সেই পটভূমিকায় সমন্বয়ধর্মী উদার মতের কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে সব মানুষই সমান। জাতপাত, অর্থ-সম্মান দিয়ে মানুষকে যাচাই করা ঠিক নয়। তাদের সেই উদার সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারার প্রতিফলন এই মেলায় উপলব্ধি করে আমার মনটা ভরে গিয়েছিল। আমিও এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েছি। তৃতীয়ত, আমার মধ্যে যে অহংকার ও কুসংস্কার অনেকদিন ধরে বিভিন্ন পরম্পরায় বর্তমান ছিল তা যেন এই মেলায় এসে একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেল।
উপসংহার: মেলা যেহেতু মিলন সাধনার ক্ষেত্র, তাই এই মেলায় আমার সেই মিলনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে মুক্তির দিশা দিয়েছে। নদীমাতৃক সভ্যতায় যে কত সুন্দর উপাদান রয়েছে অজয়ের তীরে বাউলের গানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেইসব উপাদান আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, নাড়িয়ে দিয়েছে আমার চেতনাকে তাই চেতনার উন্মীলনে এই মেলা আমার জীবনের স্মৃতিকোঠায় চিরদিন অম্লান রূপে সঞ্চিত থাকবে।
দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান / প্রত্যাহিক জীবনে বিজ্ঞান:
দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান
➯ভূমিকা: আধুনিক জীবনে যুক্তিবোধ ও কার্যকারণ পরম্পরা জ্ঞান থেকেই শুরু হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আর এই চলচ্চিত্র ঠিকই প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান মানুষকে উপহারস্বরূপ দিবে সেই মধ্যযুগের কুসংস্কার থেকে মুক্ত আর দিল জগত জীবনের প্রতি এক আলাদা মায়া। এই মায়া মমতা থেকে যে শুধু দেবতারাই করতে পারে – এই বোধ সবার কাছ থেকে অপসারিত হল, তার জায়গায় এলস মহাজগতের মানুষের অসাধারণ মহিমার প্রতি আস্থা। মানুষ আর শুধু শুধু দেবতার উপর ও প্রকৃতির উপর ভরসা করে না থেকেই তার বিকল্প সন্ধান করতে শুরু করল। আর এভাবে ক্রমাগত বিকল্প সন্ধান করতে করতে মানুষ তার প্রত্যাহিক বা নিত্য – প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারকে গ্রহণ করতে শুরু করল। অবশ্য এটাও ঠিক যে, দৈনন্দিন বা ব্যবহারক জীবনে বিজ্ঞান কে গ্রহণ করার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠল।
➯প্রত্যাহিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব: বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত একটি মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিশেষভাবে রয়েছে। প্রত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অস্তিত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই মানুষের কাছে। প্রত্যাহিক জীবনচর্চার, অফিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি প্রায় সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে।
➯বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান: প্রত্যাহিক জীবনকে আমরা যদি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিজ্ঞানের অবদান আলোচনা করি তাহলে আমরা জানতে পারবো যে বিজ্ঞানকে আমরা জানতে বা অজান্তে কতটা গ্রহণ করছে। প্রতিদিনের গৃহকার্য শুরু করে, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। প্রত্যহিক জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব অতুলনীয়।
➯অফিস আদালতে বিজ্ঞানের প্রভাব: অফিস আদালতেও সাধারণত কম্পিউটার, ইমেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারি। আর যার ফলে অফিস আদালতের কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।
➯শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব: বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব বা অবদান অতুলনীয়। বর্তমানে ছাপাখানার দরুন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ করতে পারে। আবার যে বই খুব সহজে পাওয়া যায় না সেই বইয়ের পাতা জেরক্স করেও নেয়া যাচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখন যেকোনো বিষয়ে ভালোভাবে জানতে পারছে এবং তার মাধ্যমে আবার দেশ বিদেশের খবর খুব সহজে জানা সম্ভব হচ্ছে।
➯কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব: প্রত্যহিক জীবনে কৃষিতে যে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে তাও বিজ্ঞানের প্রভাবে। আমাদের দেশের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে সাধারণ মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে এক সবুজ বিপ্লবের দরকার ছিল। আগে যে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত আমাদের সমাজ ছিল, বর্তমানে তার নেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে। কারণ প্রত্যাহিত জীবনে মানুষের আর খাবারের অভাব নেই।
➯গৃহকাজে বিজ্ঞানের প্রভাব: আগে নিত্য প্রতিদিনের গৃহ কাজে বাড়ির মা ও বোনেরা ঘর ঝাড় দিতো, মসলা বাটতো, কাপড় কাচ তো, খড় কেটে গরুকে দিত, উনুনে ফু দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করত। আর এখন বিজ্ঞানের প্রভাবে তার বিকল্প এসেছে সমাজ, ঘর পরিষ্কার করা মেশিন, মিক্সি, ওয়াশিং মেশিন, খড় কাটা মেশিন, গ্যাসের উনুন, ফ্রিজ ইত্যাদি।
➯কুফল: প্রত্যাহিক জীবনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সমাজ উন্নত হতে পেরেছে কিন্তু বিজ্ঞানের যে কুফল গুলি বা খারাপ দিকগুলির এখনও মানুষ দূর করতে পারেনি। তাই তো বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে তো বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে মানুষের আবেগ। মানুষ যে পরস্পর নির্ভর করে সামাজিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে জীবন-যাপন করতো তার নেই সবই কৃত্রিম হয়ে রইল সমাজে। যে রাসায়নিক স্যার ও কীটনাশক দিয়ে ক্রমবর্ধমান বর্ধিত জনসংখ্যার মুখে খাবার তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে মানুষেরা হচ্ছে বিভিন্ন রোগের দ্বারা ভুক্তভোগী।
➯উপসংহার: সুতরাং দৈনন্দিন জীবনের যেদিকেই তাকাই না কেন বিজ্ঞানের প্রভাব কে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু অতিমাত্রায় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত যন্ত্র কে ব্যবহার করে ক্রমাগত মানুষ হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক। কৃত্রিম মানুষ তাই বিজ্ঞানের ভালো দিক থেকে কাজে না লাগিয়ে খারাপ দিক থেকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের নিত্য প্রতিদিনের জীবনে। ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে অমানুষ, আর ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠছে স্বার্থপর। অবশ্য এই স্বার্থপরতার কারণ বিজ্ঞান নয় – বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।
এই রচনাকে অনুসরণ করে যে রচনা গুলি লেখা যাবে :-
১) প্রত্যহিক জীবন ও বিজ্ঞান
২) ব্যবহারিক জীবন ও বিজ্ঞান
৩) বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবন
প্রত্যাহিক জীবনে পরিবেশের ভূমিকা:
প্রত্যাহিক জীবনে পরিবেশের ভূমিকা
ভূমিকা: Nature যে আমাদের Natural করে সেকথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অবস্থা দেখে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। কেননা, মানবজীবনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অঙ্গালী। আমরা জানি, ‘বনে থাকে বাঘ, গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ’ অর্থাৎ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বেঁচে থাকার উপরে পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া তথা বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি বজায় থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা অভিজেন গ্রহণ করি এবং পরিবেশকে আমর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফিরিয়ে দিই। পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে আমরা খাদ্যগ্রহণ করে বেঁচে থাকি। পরিবেশের জল, বায়ু, অরণ্য আমাদের জীবনধারণের রসদ যোগায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘আরণ্যক’ ও ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ না বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর যে রয়েছে তা বলাবাহুল্য।
পরিবেশের সংজ্ঞা: মানুষকে ঘিরে যাবতীয় জড় ও সঞ্জীব উপাদানগুলিকে একত্রে পরিবেশ বলে। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের সামগ্রিক ভৌত ও জৈব পরিবেশের আস্তারিয়ায় সৃষ্ট অবস্থ আমাদের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে, তাকে পরিবেশ বলা হয়। আমাদের প্রত্যেকের বাসস্থানের চারদিকে অবস্থিত জড় উপাদান—জল, বায়ু, মাটি, সূর্যালোক, উন্নতা ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এগুলি ভৌত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।
পরিবেশের স্বরূপ: পরিবেশকে আমরা সাধারণত দুটো রূপে দেখতে পাই। যেমন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ আলো, বাতাস, জল, মাটি, পাহাড়-পর্বত, সাগর মহাসাগর, নদ-নদী, হ্রদ, জলাশয়, ঝরণা, বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি মেরু অঞ্চল, তৃণলতা, গুল্ম, বৃক্ষ, কাট-পালা, পশুপাখি, আণুবীক্ষণিক জীবসহ যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। আবার ভৌগোলিক গঠন, জলবায়ু ও উষ্ণতার তারতম্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—জলজ এবং লজ পরিবেশ। অন্যদিকে কৃত্রিম পরিবেশ হল মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ। এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি। এই সমস্ত পরিবেশের প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে।
প্রাকৃতিক পরিবেশ: মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মানুষ জল, অক্সিজেন, খাদ্যই গ্রহণ করে না; মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এই পরিবেশের প্রভাবজাত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত জলজ পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। স্থলজ পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমতলের পরিবেশ, অরণ্যের পরিবেশ, পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ, মরু অঞ্চলের পরিবেশ, মেরু অঞ্চলের পরিবেশ।
পারিবারিক পরিবেশ: কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশ বা বাড়ির পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি। জন্মের পর থেকেই শিশুরা মা ও বাবার যত্নে পালিত হয় এবং তাদেরকেই ভালোভাবে চিনতে বা জানতে শেখে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়ির কাছের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে গৃহস্থালীর কাজ, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা অনুকরণ করতে শেখে। বড়োদের কাছ থেকে নীতিমূলক উপাখ্যান শুনে তাদের কল্পনাশক্তির যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি ন্যায়-নীতি বোধও জাগ্রত হয়। আবার গুরুজনদের অশালীন আচরণ ও ব্যবহারও তারা অনুকরণ করে ফেলে। তবে বাড়ির গুরুজনদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুদের চরিত্র, আচার-আচরণ প্রভৃতি গুণাবলীর উন্মেষ শিশুমনে ঘটতে থাকে।
বিদ্যালয়ের পরিবেশ: পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু যেমন আহরণ করে, তেমনি বড় হয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও শিশুরা তাদের চারিত্রিক গুণাবলী আয়ত্ত করে। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুকে সাহায্য করে। এই পরিবেশ থেকেই শিক্ষার্থীদের সততা, শ্রদ্ধাভক্তি, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে।
সামাজিক পরিবেশ: একজন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সমাজে নানা বিষয়ে বা কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সে সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতির শিক্ষা হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব, তাই পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কিম্বা সমাজকল্যাণের বা সমাজের জন্য নিজেদেরকে ত্যাগ করার ইচ্ছা তৈরি হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে। সেজন্য মানবজীবনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সর্বাধিক।
সাংস্কৃতিক পরিবেশ: এরপরে আসে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবের দিক—যে পরিবেশ থেকে একজন মানুষ সভ্য নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করে। বিদ্যালয়ে ও সমাজে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দেশ ও জাতি সম্পর্কে একটা চেতনা জাগে।
পরিবেশ দূষণ: মানুষ পরিবেশ থেকে যেমন নিয়েছে, তেমনি পরিবেশকে দূষিতও করেছে। সেই দূষণের প্রভাব আজ সর্বত্র। জল, বায়ু, আকাশ, শব্দ, মাটি সবই আজ দূষণের করল গ্রাসে পতিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশও আজ দুষিত। মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতিহীনতা, সুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতার ছড়াছড়ি মানুষের সামাজিক সম্পর্কে এনেছে ভাঙনদশা। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্র-সর্বস্ব, কৃত্রিম ও আন্তরিকতাবিহীন। ফলে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ আজ ভূলুণ্ঠিত।
উপসংহার: যে পৃথিবী মানুষের বসবাসের একমাত্র আবাসস্থল, সেই পৃথিবী আজ নানাভাবে দূষিত। অথচ এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে মানুষ পেয়েছিল প্রাণধারণের রসদ, অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণ। কিন্তু নিতে নিতে মানুষ আজ ভুলে গেছে তার চারপাশের পরিবেশকে। ফলে পরিবেশের দূষণের প্রভাবেও মানুষ আজ অতিষ্ঠ। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে এই পরিবেশকে বাচিয়ে রাখার। তা না হলে অস্তিত্ব হবে, পরবর্তী প্রজন্মের ‘দুধে-ভাতে’ থাকার স্বপ্নও বিলীন হয়ে যাবে।
অনুসরণে লেখা যায় :
- আমাদের পরিবেশ ও আমরা।
- আমাদের জীবনে পরিবেশের ভূমিকা।
বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ:
বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ
ভূমিকা: বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও, এর সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজ্ঞানের প্রচুর অবদান সত্ত্বেও, মানুষের জীবনে এটির প্রভাব কীভাবে পড়ছে—এ প্রশ্ন এখনও বিতর্কের বিষয়। যেখানে একদিকে বিজ্ঞান মানবকল্যাণে বিপুল অবদান রেখেছে, অন্যদিকে এর ব্যবহারে সৃষ্ট বিপদও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কি আমাদের মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? বিজ্ঞান কি শুধুই প্রগতির পথ দেখাচ্ছে, নাকি মানবজাতিকে যান্ত্রিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে? এ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল উভয় দিক বিশ্লেষণ করতে হবে।
বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল: বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে প্রগতির এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে। এর সুফলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যোগাযোগ, চিকিৎসা, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট আমাদের তথ্য আদান-প্রদানকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেমন মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার বা হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপনের মতো জটিল কাজ আজকের দিনে সম্ভব হয়েছে, তেমনি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে স্যাটেলাইট চিত্র, টেলিভিশন, এবং আবহাওয়া পূর্বাভাস সংগ্রহ করে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছি। শিল্প ও কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের পরিশ্রম লাঘব করেছে এবং খাদ্য উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি এনেছে।
তবে, বিজ্ঞানের কুফলও কম নয়। পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহারে হিরোসিমা ও নাগাসাকির মতো ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে, যা আজও মানবসভ্যতার এক কালো অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয়। রাসায়নিক অস্ত্র, যুদ্ধবিমান, এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মতো মারণাস্ত্রগুলি মানবজীবনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া, প্রযুক্তির অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলছে, যা সম্পর্কের মধ্যে ঠাণ্ডা দূরত্ব সৃষ্টি করছে এবং সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে নষ্ট করছে। পরিবেশ দূষণ, বিশেষত শিল্পাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বনভূমি ধ্বংস, এবং বায়ুদূষণও বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ফল। বিজ্ঞানের এই কুফলগুলি আমাদের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে এবং তাই এর সঠিক ব্যবহার আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
প্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান: আগুন জ্বালানোর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের যে যাত্রা শুরু, তা একের পর এক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে। ছাপার মেশিনের আবিষ্কার যেমন শিক্ষার বিস্তারে বিশাল ভূমিকা রেখেছে, তেমনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যেমন মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, এবং ল্যাবরেটরির ব্যবহার উচ্চতর শিক্ষাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। ব্রেইল পদ্ধতি অন্ধদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা আজকের দিনেও শিক্ষার্থীদের অমূল্য সহায়ক। স্বাস্থ্য খাতে, বিশেষ করে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার ও হৃদপিণ্ড পরিবর্তনের মতো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন ইনস্যাট সিরিজ আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিয়েছে, সেই সাথে দূরদর্শন এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিপুল অবদান রেখেছে। প্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই সমস্ত অবদান শুধু আমাদের জীবনকে সহজ করেনি, বরং সভ্যতার অগ্রগতির পথে এটি একটি অনিবার্য সহায়ক।
সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব: সভ্যতার প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ আজকের দিনে অবিস্মরণীয়। গ্রাম বাংলার পথঘাট থেকে শুরু করে শহরের উঁচু দালানকোঠা পর্যন্ত—বিজ্ঞানের উপস্থিতি সর্বত্র। কৃষিতে পাওয়ার টিলার ও রাসায়নিক সার, শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক যানবাহন—এসবই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। কিন্তু শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়; বিজ্ঞানের দান পৌঁছে গেছে আমাদের বিনোদন, শিক্ষা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায়। এতদিন অরণ্য, সমুদ্র, বা হিমবাহে পৌঁছানো যেখানে স্বপ্ন ছিল, বিজ্ঞান সেটিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তবে বিজ্ঞানের এই উন্নতি সব ক্ষেত্রেই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে এটি মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, হিংসা, এবং পরশ্রীকাতরতা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই, বিজ্ঞানের অপব্যবহার রোধ করে এর সুফলগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই এখন জরুরি।
শান্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা: বিজ্ঞান তার আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে মানবজীবনে যে শান্তি ও স্বস্তি এনেছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর পাশাপাশিই বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রগুলো, যেমন পরমাণু বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্র, মানবজাতির জন্য এক বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বিজ্ঞান তার সামর্থ্য দিয়ে কীভাবে মানবজাতির বিনাশ ঘটাতে পারে। তবে, বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করলেও এর প্রকৃত ব্যবহারকারীই এর জন্য দায়ী। আজকের দিনে বিজ্ঞানকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে নয়, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত করা উচিত।
উপসংহার: বিজ্ঞানের আশীর্বাদ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অভিশাপও। আমরা বিজ্ঞানের অপব্যবহারকে দায়ী করতে পারি না, বরং আমাদের লোভ এবং অসচেতনতা এর জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, যন্ত্রের অপব্যবহার আমাদের মানবতাকে ধ্বংস করে দেয়। জীবনকে সুন্দর এবং মানবিক রাখতে হলে বিজ্ঞানের শক্তিকে সদ্ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞান যদি মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়, তবে এটি হবে আমাদের সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে, এর কুফলগুলি দূর করে এর সুফলগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। তাই, বিজ্ঞানের শক্তি তখনই প্রকৃত আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন এটি মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হবে।
একটি গাছ একটি প্রাণ:
একটি গাছ একটি প্রাণ
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেছিলেন, “মানুষের শক্তি যদি প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কারণ প্রকৃতির সহজ নিয়ম অতিক্রম করলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিনাশ অনিবার্য।” এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানব সভ্যতা নিজের স্বার্থে প্রকৃতিকে নির্বিচারে শোষণ করে চলেছে। এর ফলে আমরা প্রাকৃতিক দূষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো বৃক্ষরোপণ। কারণ “একটি গাছ একটি প্রাণ” — এই সত্যকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।
জীবমণ্ডলে উদ্ভিদের গুরুত্ব: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল, এবং জলমণ্ডলকে কেন্দ্র করে যে জীবমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্ভিদের দ্বারা প্রাণীকুলের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রাচীন কালে, পৃথিবীতে অক্সিজেন ছিল না। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভাগ বাড়তে শুরু করে, যা অন্যান্য জীবের জন্ম ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। আজকের পৃথিবীতে মানুষ, পশু, এবং পাখি, সবই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ শুধু অক্সিজেন সরবরাহ করে না, তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং খাদ্যের মূল উৎস হিসেবে কাজ করে।
গাছ ও অরণ্য রক্ষার গুরুত্ব: উদ্ভিদ আমাদের জীবনধারণের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গাছপালা আমাদের জন্য খাদ্য, অক্সিজেন, ওষুধ এবং জ্বালানির উৎস। তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং আবহাওয়ার সমতা রক্ষা করে। বনভূমির উপস্থিতি মাটি থেকে জল শোষণ এবং তার পুনঃপ্রবাহে সহায়তা করে, যা বৃষ্টির জল জমা করে এবং বন্যা প্রতিরোধ করে। বনভূমির গাছপালা জলচক্র, কার্বন চক্র, এবং অক্সিজেন চক্রকে সক্রিয় রাখে, যা মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য।
অরণ্য ধ্বংসের স্বরূপ ও কারণ: অরণ্য ধ্বংসের পেছনে রয়েছে মানুষের অপরিকল্পিত কার্যকলাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অধিক জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে, যা বনভূমির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। কাঠের চাহিদা বাড়তে থাকায়, বনভূমি ক্রমশ ধ্বংস হচ্ছে। “গ্রীন হাউস এফেক্ট” এর ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা উদ্ভিদজগৎকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। হিমালয় অঞ্চলে গ্লেসিয়ার গলে যাওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এসবের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং মানবজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।
বন ও গাছ রক্ষায় আমাদের করণীয়: এই সংকটের সমাধানে প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রথমত, বনভূমি রক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পতিত জমিতে বনসৃজন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। তৃতীয়ত, জ্বালানি হিসাবে কাঠের বিকল্প ব্যবহার প্রচলিত করা উচিত। চতুর্থত, সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পঞ্চমত, বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বনভূমির সংরক্ষণ ও পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে হবে। এছাড়া, শহরের মানুষদেরও সচেতন করা উচিত, যারা নগরায়নের জন্য বনভূমি ধ্বংস করছে।
উপসংহার: সচেতনতা এবং সমন্বিত পদক্ষেপই পারে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে। আমাদের সকলের উচিত শপথ নেওয়া— “একটি গাছ একটি প্রাণ” এই বিশ্বাস নিয়ে প্রতিটি মানুষকে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করা। বৃক্ষের সুরক্ষা ও বৃদ্ধি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্য, বৃষ্টি, এবং প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য গাছই আমাদের একমাত্র ভরসা। গাছ বাঁচলে, বাঁচবে প্রাণ, বাঁচবে পৃথিবী।
সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা:
সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা
ভূমিকা:- রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- “সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।” সত্যই তো, দেশকে জানা এবং নিজেকে জানার জন্য সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। আধুনিক মানুষ যত নিজেকে অপরের কাছে মেলে ধরতে চেয়েছে এবং নিজের সঙ্গে অপরের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করতে তৎপর হয়েছে ততই সংবাদপত্র সেই প্রকাশের ও উপলব্ধির সহায়ক উপকরণ রূপে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং যে কোন আধুনিক মানুষের কাছে সংবাদপত্র যে তার মনের খোরাক জোগাতে পারে – সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
সংবাদপত্রের ভূমিকা:- আধুনিক যুগের চাহিদাতেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার সংবাদপত্রের বহুল প্রচারকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে আমাদের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র মানুষের জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই তার পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সংবাদপত্র এক বিশিষ্ট মাধ্যম। এমনকি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও জাতীয়তাবোধের জাগরণে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। সেই সময়ে সংবাদপত্র শুধু খবর জুগিয়ে নয়, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে মানুষের মনে স্বাধীনতা বোধ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।
গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র:- আধুনিক যুগে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব আজ সর্বস্তরে প্রসারিত। শুধু শহর নয়, সুদূর গ্রামেও কোন চা-এর দোকানে সংবাদপত্র পাঠের জন্য মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। রাজনীতি থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সব শ্রেণির সংবাদ, সংবাদপত্র থেকে মানুষ গ্রহণ করে নিজেদেরকে আলোকিত করে। রাজনীতি, খেলাধুলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় খবর পাওয়ার জন্য সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। দেশবিদেশের নানান খবরের আলোকে আধুনিক মানুষ নিজেকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং তা সম্ভব সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে। শুধু শিক্ষার জন্য নয়, জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে সংবাদপত্র পাঠ একান্ত জরুরি।
দৈনিক সংবাদপত্র:- প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একজন সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন সংবাদপত্র পড়ে পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। তাছাড়া সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা, জনমত গঠন করা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত করা প্রভৃতি। সেদিক থেকে একজন আধুনিক মানুষকে সাহায্য করতে পারে সংবাদপত্র ।
পড়ুয়াদের কাছে সংবাদপত্র:- শিক্ষার্থীদের কাছে, সাধারণ স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের কাছে সংবাদপত্র বিশেষ আকর্ষণ। পাঠ্য বহির্ভূত কোন খবর জানতে, পাঠের একঘেয়েমি দূর করতে, সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে, নান্দনিক বোধের ভান্ডার গড়ে তুলতে, নিজস্ব চেতনার বিস্তার ঘটাতে, পাঠে মনোনিবেশ আনতে শিক্ষার্থীদের কাছে সংবাদপত্র পাঠ একান্ত জরুরি। বিশেষ করে আজকাল কোন কোন সংবাদপত্রে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ও প্রশ্নোত্তরের যে সব কলম থাকে তাতে শিক্ষার্থীরা যে বিশেষ উপকৃত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
সৃজনধর্মী বিকাশে সংবাদপত্র:- সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে যে কোন মানুষ তার নিজস্ব মত প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক সমীপেষু কলমে তাঁর মতামত লিখে জানাতে পারেন। তাই সংবাদপত্র সেদিক থেকেও মানুষের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভাকে উন্মেষিত করতে সাহায্য করতে পারে। এই সৃজনধর্মিতার বিকাশে সংবাদপত্র পাঠ যে জরুরি, সে বিষয়ে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন না।
নেতিবাচক দিক:- একথাও ঠিক যে, আজকাল সংবাদপত্রে যেসব নেতিবাচক দিক অর্থাৎ খুন-জখম, দুর্বৃত্তায়ন, রাজনীতির উত্তপ্ত আবহাওয়া প্রভৃতি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে সংবাদপত্র তার পুরোনো সার্বিক গুরুত্বকে হারাচ্ছে তা বলাবাহুল্য। তবুও সংবাদপত্রের সেই ব্যবসায়িক দিক বাদ দিলে তার পাঠের গুরুত্ব যে অপরিসীম—সেকথা সকলেই স্বীকার করবেন।
উপসংহার:- শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন — থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়।” সেকথাকে একটু পরিবর্তন করে বলা যায়, সংবাদপত্র পাঠে লোকশিক্ষা হয়। তাই সংবাদপত্র পাঠ আজকের দিনে যে কোন মানুষের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছে। সেজন্য সুদূর গ্রামাঞ্চলেও মানুষ ঘুম ভেঙে খবরের কাগজে চোখ রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অবসর বিনোদনের জন্যও সংবাদপত্র এক অনন্য মাধ্যম রূপে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং জনমত গঠনে, মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশে, সৃজনীশক্তির উদ্ভাবনে, অবসর বিনোদনে এবং নিজেকে ও অপরকে জানতে, “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে’ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর জীবনী:
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ভূমিকা: টেনিদাকে চেনেন না এমন বাঙালির সংখ্যা খুব কম। তার সাহিত্যকীর্তি এর জন্য তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি একজন নাট্যকার,সাহিত্যকার,প্রবন্ধীক। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন রোমান্টিক লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন।
জন্ম ও শিক্ষা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গিতে ১৯১৮ সালের ৮ ফ্রেব্রুয়ারি। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পুলিশ অফিসার। বাবার বদলির চাকরি হওয়ার কারণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পড়াশোনা দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল এবং কলকাতায় সম্পন্ন হয়। তাঁর আসল নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর রচনাকর্মে আসল নামের পরিবর্তে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাম ব্যবহার করেন।
➯ স্কুলের পড়াশোনা নারায়ণ শুরু করেন ১৯৩৩ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে। তারপর তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন ১৯৩৬ সালে। ওই একই কলেজ থেকে তিনি কলা বিভাগে স্নাতক হন (১৯৩৮ সালে)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ (বাংলা) পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৯৪১ সালে ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক এবং ‘সাহিত্যে ছোটোগল্প’ বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৬০ সালে ডিফিল উপাধি লাভ করেন।
কর্মজীবন: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুবিধ কৃতিত্বের অন্যতম হল শিক্ষকতা। তিনি বেশ কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন যার মধ্যে রয়েছে আনন্দচন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি (১৯৪২-৪৫), সিটি কলেজ, কলকাতা (১৯৪৫-৫৫)। পরে ১৯৫৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন।
সাহিত্যকীর্তি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার শুরু তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই। রুমে রুমে ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্পটির নাম “বিচিত্রা”। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমন একজন লেখক ছিলেন যে তাঁর সাহিত্যকর্মে দেশপ্রেম ও রোমান্স-এর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘উপনিবেশ’ সুন্দরবনের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত, যখন ‘সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী’, ‘মহানন্দা’ ও ‘লালমাটি এক উপজাতির ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্বেষণমূলক উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে পড়ে ‘শিলালিপি’, ‘পদসার’, ‘বৈতালিক’ প্রভৃতি এবং অতি অবশ্যই তাঁর কিশোর রচনাসম্ভার, যার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে টেনিদার কান্ডকারখানার অনাবিল হাসি আর রস সমৃদ্ধ গল্প, উপন্যাস ‘চারমূর্তি’, ‘পটলডাঙার টেনিদা’ প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলিও বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অমূল্য সম্পদ, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হল, ‘লক্ষ্মীর পা’, ‘ইতিহাস’, ‘হাড়’, ‘বিতংস’, ‘বনজ্যোৎস্না’ ‘তাস’, ‘হরিণের রং’ ইত্যাদি। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি প্রধানত দুটি জার্নাল লেখায় মনোনিবেশ করেন, যাদের একটির নাম- সুনন্দর জার্নাল’।
মৃত্যু: মাত্র ৫২ বছর বয়সে ৬ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে কলকাতায় মৃত্যু বরণ করেন, বাংলার এই কীর্তিমান সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
উপসংহার: একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও শিক্ষক হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিরদিনের জন্য পাঠক ও তার ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার পাণ্ডিত্য,অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ ছিল তীক্ষ্ণ ও সজীব তাই তার লেখা যেমন ক্ষুরধার তেমনি সহজ ও সাবলীল।
বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য:
বাংলার ঋতু বৈচিত্র
ভূমিকা: বাংলার প্রকৃতি ঋতুর মাধুর্যে ভরপুর। এখানে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে প্রকৃতির রূপও বদলে যায়। প্রতিটি ঋতু নতুন করে বাংলার মাটিকে সাজায়, আর সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় বাংলার মানুষ। কবিগুরুর ভাষায়, “বাহিরে রয়েছে প্রকৃতির মুকুল, ভিতরে রয়েছে হৃদয়ের মুকুল”—এই হৃদয়ের মুকুল ফুটিয়ে তোলে বাংলার ঋতুগুলো।
গ্রীষ্ম ঋতু: বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল পশ্চিমবঙ্গে তার পদার্পণ করে। তীব্র সূর্যের তাপে বাংলার মাটি শুকিয়ে যায়, নদী-নালা, পুকুর-দীঘি যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই তাপেই পেকে ওঠে আম, লিচু, তরমুজের মতো রসালো ফল। গ্রামবাংলার মেঠোপথে খেজুরের রস আর তালপাখার বাতাসে খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণে সজীবতা ফিরে আসে।
বর্ষা ঋতু: আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষাকালের জন্য। বাংলার আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা আর মাটির বুকে বৃষ্টির ধারা নবজীবনের বার্তা বয়ে আনে। কৃষকরা তাদের জমিতে বীজ বপনে মগ্ন হয়, আর নদীগুলো আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। বর্ষাকালের আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে দুঃখও—অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বন্যা, ফসলের ক্ষতি এবং রোগব্যাধির প্রকোপ। তবুও, এই বর্ষা কৃষিনির্ভর বাংলার কৃষকের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।
শরৎ ঋতু: ভাদ্র-আশ্বিন মাস শরৎকাল। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশফুলের দোলায় বাংলার প্রকৃতি সাজে। শরতের সোনালি আলো, শিউলি ফুলের গন্ধ, আর দেবী দুর্গার আগমনের বার্তা বাংলার মানুষের মনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। প্রকৃতি ও মানুষ একত্রে মিলেমিশে এই সময়টাকে উদযাপন করে।
হেমন্ত ঋতু: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে হেমন্তের আগমন। শরতের মাধুর্যের পর হেমন্ত আসে পূর্ণতা ও মঙ্গলের বার্তা নিয়ে। বাংলার কৃষকের গোলা ভরে ওঠে সোনালী ধানে। নবান্নের উৎসব, নতুন ধানের ঘ্রাণ, সবমিলিয়ে হেমন্ত যেন বাংলার মাটিকে আরও উর্বর করে তোলে।
শীত ঋতু: পৌষ-মাঘ মাস শীতের প্রকোপের সময়। বাংলার শীতকালে কুয়াশায় ঢাকা সকাল, মৃদু ঠাণ্ডার হাওয়া, আর পিঠেপুলির গন্ধ বাংলার মানুষকে উষ্ণতার স্বাদ দেয়। শীতকালে বিভিন্ন শাকসবজি আর ফুলের সমারোহ বাংলার প্রকৃতিকে সৌরভমণ্ডিত করে। এই ঋতুতে বাঙালি সমাজ বিভিন্ন মেলায় মেতে ওঠে, আর শীতের আমেজ উপভোগ করে।
বসন্ত ঋতু: ফাল্গুন-চৈত্র মাস নিয়ে বসন্তকাল। এই ঋতুতে প্রকৃতি যেন নববধূর মতো সেজে ওঠে। গাছে গাছে নতুন পাতার কিশলয়, পলাশ-শিমুলের রঙে সেজে ওঠে বনভূমি। কোকিলের কুহু ডাক আর মধুমাসের হাওয়া বাঙালির মনে প্রেমের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। বসন্ত উৎসব আর দোলযাত্রা এই ঋতুর বিশেষ আকর্ষণ।
ঋতুবৈচিত্র্যের প্রভাব: বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য বাংলার কৃষি, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ঋতু নতুন ধরনের ফসল, পোষাক, এবং উৎসব নিয়ে আসে। ঋতুবৈচিত্র্যের এই রঙিন চিত্র বাংলা সাহিত্যে, সংগীতে, এবং শিল্পকলায় বারবার ফুটে উঠেছে। কবি, লেখক, শিল্পীরা তাদের রচনায় বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন।
উপসংহার: বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য প্রকৃতির এক অসামান্য উপহার, যা বাংলার মানুষকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপে মুগ্ধ করে। কিন্তু, পরিবেশের ক্রমাগত অবনতি ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই ঋতুগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। তাই, আমাদের উচিত এই ঋতুগুলির মাধুর্য এবং বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মও এই প্রকৃতির রূপের সাথে পরিচিত হতে পারে।
দ্বিশত জন্মবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত:
দ্বিশত জন্মবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যজগতে মহাকবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব আকস্মিক অথচ যুগোপযোগী। বাংলার ‘বাবুসমাজ’ যখন ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে ও অপরদিকে কাব্যরসিক সমাজের রসবোধ পয়ার-ত্রিপদী আস্বাদনেই তৃপ্ত; এমন সময়ে যথার্থ বাংলা নাটক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ডালি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন যুগস্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
জন্ম ও বংশ পরিচয় : বাংলার মহাকবি মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন বিদুষী ও স্নেহময়ী রমণী।
শিক্ষা জীবন : মধুসূদন দত্তের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামে মায়ের কাছে, তারপর গ্রামের পাঠশালায়। সাত বছর বয়স হলে পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে নিজের কাছে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং খিদিরপুর স্কুলে ভরতি করে দেন। এর দু-বছর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের সর্বনিম্ন শ্রেণিতে ভরতি হন। সেইসময় ব্রিটিশ- শাসিত ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান ছিল হিন্দু কলেজ।
কর্ম জীবন : এখানেই মধুসূদন সহপাঠী হিসেবে পান বঙ্গগৌরব ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখকে। হিন্দু কলেজের আকাশের একঝাক তারার মধ্যে তিনি ছিলেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সেই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে কবিচেতনার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতা কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবকেও মুগ্ধ করে। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ইংরেজি কাব্যরচনা, মহাকবি হওয়া ও বিলাত-যাত্রার স্বপ্ন দেখতেন। তাই বাড়িতে তাঁর বিবাহ উদ্যোগ শুরু হলে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হিন্দু কলেজ ছেড়ে বিশপস্ কলেজে ভরতি হন তিনি। মধুসূদন দত্ত বাংলা, সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।
হিন্দুর ছেলে হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন পিতা। তখন অর্থসাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়। তাই জীবিকার্জনের তাগিদে তিনি মাদ্রাজে গিয়ে ‘মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম’ ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও চলতে থাকে।
বিবাহ জীবন : ৩১ জুলাই ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহ চিরস্থায়ী হয়নি। তাই মধুকবি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন সিলি হেনরিয়েটাকে। পিতার মৃত্যুর পর স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ কোর্টে কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করে পরে দ্বিভাষিকের কাজ পান।
সাহিত্যচর্চা : মধুসুদন দত্তের ইচ্ছা ছিল বায়রনের মতো ইংরেজি ভাষায় সুকবি হওয়ার। তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেন, তবে তাতে মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে থাকার সময় তিনি ‘Timothy Penpoem’ ছদ্মনামে ‘A vision of the Past’ ও ‘Captive Ladie’ নামক ইংরেজি কাব্য রচনা করেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে কবি এর একটি কপি জে ই ডি বেথুন সাহেবকে পাঠালে তিনি কাব্যটির প্রশংসা করেন। তবে ইংরেজির বদলে তাঁকে বাংলা ভাষাতেই কাব্য রচনা করার পরামর্শ দেন। বন্ধু গৌরদাস বসাকও তাঁকে একই কথা বলেন। এর পরবর্তীকালে তাঁর পরভাষায় কবিখ্যাতি অর্জনের মোহভঙ্গ ঘটলে তিনি মাতৃভাষায় কাব্য ও নাটক রচনা শুরু করেন।
মধুকবি নাট্যরসিক ছিলেন। কলকাতার বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত ‘রত্নাবলী’ নাটক দেখে মধুসুদন লেখেন-
“অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।”
এরপরই তিনি যথার্থ বাংলা নাটক রচনায় অবতীর্ণ হন। লেখেন ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯), ‘পদ্মাবর্তী’ (১৮৬০), ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১) ইত্যাদি নাটক এবং ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ (১৮৬০), ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০) নামক দুটি প্রহসন। নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ (১৮৬০), ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (১৮৬১), ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ (১৮৬১), ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ (১৮৬২) ও সনেটগুচ্ছ সংবলিত ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ (১৮৬৬) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।
সাহিত্যক্ষেত্র মধুসুদন দত্তের যুগান্তকারী সৃষ্টি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা। তিনি অনুভব করেছিলেন ছেদ-যতির বন্ধনে কবিতার ভাবমুক্তি যথাযথ হয় না। তাই তিনি চোদ্দো মাত্রার বন্ধনেই কবিতাকে আবদ্ধ রাখলেন কিন্তু ছেদ-যতির বন্ধন খুলে ভাব অনুসারে কবিতার ছন্দকে মুক্তি নিয়ে নতুন ধারার কবিতা রচনায় সক্ষম হলেন।
বিলেত যাত্রা : শুধু বিলেতি ধাঁচে সাহিত্যরচনাই নয়, মধুকবির মনে বিলাতি শিক্ষাগ্রহণের বাসনাও ছিল। তাই তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। কবি ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফেরেন ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি।
শেষ জীবন : আজীবন অমিতব্যয়ী কবি শেষজীবনে অত্যধিক অর্থকষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হন। এইসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন বলে জনশ্রুতি আছে। পত্নী হেনরিয়েটার মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পরে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। আশার ছলনায় পথভ্রষ্ট, এক স্বপ্নময় বাঞ্ছিত তৃপ্তির পশ্চাতে আজীবন ধাবিত, অতৃপ্ত এক মহামানবের নাম কবি শ্রীমধুসূদন।
![]()